[পরিমার্জিত]
[ভিডিও লিংক: বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় মিশনারী- গোড়া ও ডালপালাঃ শায়খ মুসা আল হাফিজ]
পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, সেগুলো প্রচারের দিক থেকে দুই রকম। যথা:
১) যে ধর্ম সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বাইরে প্রচার করা যায়;
২) যে ধর্ম সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বাইরে প্রচার করা যায় না।
এখন, খ্রিষ্ট ধর্ম আসলে কোন প্রকারের মধ্যে পড়ে তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ বলে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রথম প্রকারের, অর্থাৎ, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বাইরে প্রচারযোগ্য; আবার অনেকের মতে এ ধর্ম দ্বিতীয় প্রকারের, অর্থাৎ, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বাইরে প্রচারযোগ্য নয়। এই বিতর্কের উৎস কী?
এই বিতর্ক আসলে জন্ম নিয়েছে খ্রিষ্ট ধর্মের উৎস থেকেই। বাইবেলে প্রচারের পক্ষে-বিপক্ষে দুই ধরনের বর্ণনা-ই পাওয়া যায়। প্রচারের বিপক্ষের কিছু বর্ণনা হলো:
১) মথির সুসমাচারে বর্ণিত আছে: যীশু খ্রিষ্ট তাঁর বারোজন সাথীকে ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব দিলেন এবং তাদেরকে আদেশ করলেন যে, “তোমরা ধর্ম প্রচার করো; তবে Gentile ( অইহুদী )-দের পথে যেওনা এবং Samaritan (ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর, তবে অইহুদী)-দের নগরে প্রবেশ করো না।” Gentile হলো যারা পরাজিত, অইহুদী। ইহুদীরা অইহুদীদের পরাজিত, নিকৃষ্ট, দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ মনে করতো। অন্যদের অধম এবং নিজেদের উত্তম মনে করতো।
ইহুদীদের মধ্যে সকল কালেই এই বিষয়টি বিদ্যমান ছিল। তারা নিজেদেরকে Chosen People মনে করতো। কুরআনের মধ্যে বর্ণিত আছে: “আর ইহুদীরা বলে, ‘উযাইর আল্লাহর পুত্র’ এবং নাসারারা বলে, ‘মাসীহ আল্লাহর পুত্র’।” [আল-কুরআন, (৯:৩)] ইহুদীরা এ কথাও দাবি করেছে: “… আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর নিকট অধিক প্রিয়।” [আল-কুরআন, (৫:১৮)]
২) মথির সুসমাচারে দেখা যায়: যীশু খ্রিষ্ট বলছেন যে, “তোমরা তোমাদের পবিত্র বস্তু কুকুরদেরকে দিও না এবং তোমাদের মণি-মুক্তা শূকরের সামনে ফেলো না। কারণ শূকর এটিকে ময়লা করে ফেলবে, পদতলিত করে ফেলবে এবং পরবর্তীতে তোমাকে আক্রমণ করবে। ” এখানে ‘পবিত্র বস্তু’ ও ‘মণি-মুক্তা’ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বাইবেলের শিক্ষা আর ‘কুকুর’ ও ‘শূকর’ দ্বারা অইহুদী জনগোষ্ঠী উদ্দেশ্য।
৩) মথির সুসমাচারে আরো বর্ণিত: ‘কেনান’- এর অধিবাসী একজন নারী যীশুর সমীপে এসে কান্নাকাটি করছে এবং বলছে যে, আমার মেয়ের ওপর অশুভ আত্মার প্রভাব পড়েছে, আমার মেয়ের জীবন বিপন্ন। যেকোনো অসুস্থ ব্যক্তি যীশুর কাছে এলে তিনি স্পর্শের মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে দেন, এটি তাঁর ঈশ্বর প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা। কিন্তু যীশু খ্রিষ্ট সেই নারীর দিকে তাকাচ্ছেন না, তার কথাও শুনছেন না। যীশু খ্রিষ্টের অনুসারীগণ অনুরোধ করলেন যে, এই নারী অনবরত কান্নাকাটি করছে, চেঁচাচ্ছে; তার প্রতি আপনি দৃষ্টি দান করুন। তখন যীশু খ্রিষ্ট বললেন: “বনু ইসরাইলের হারানো মেষপাল ছাড়া আমি আর কারো প্রতি প্রেরিত হইনি। তাদের রেখে অন্য কারো প্রতি মনোযোগী হওয়ার অর্থ হলো নিজের সন্তানের খাবার কুকুরের পাত্রে রেখে দেওয়া।”
বাইবেলের এসকল বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, খ্রিষ্ট ধর্ম বনু ইসরাইল ছাড়া অন্য কোনো মানবগোষ্ঠীর কাছে প্রচারিত হবার ধর্ম নয়, বরং তা হচ্ছে গোত্রভিত্তিক ধর্ম, যা ইসরাইল গোত্রের জন্য সীমাবদ্ধ।
আবার, প্রচারের পক্ষের বর্ণনা হলো: মার্কের সুসমাচারে বর্ণিত আছে যে, কবর থেকে পুনরুত্থানের পর যীশু বললেন যে, “তোমরা গোটা জগতে ছড়িয়ে পড়ো এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের সামনে সুসমাচার প্রচার করো, আমার সত্যবাণী প্রচার করো।” বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী, এই কথা তিনি পুনরুত্থানের পরে বলেছেন।
এই ঘটনার ওপর ভিত্তি করে St. Paul এবং St. Peter জোরালোভাবে দাবি করলেন যে, খ্রিষ্ট ধর্মের স্থায়িত্বের জন্য বনু ইসরাইলের বাইরে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কাছে এই ধর্ম প্রচার করতে হবে। সেসময় খ্রিষ্ট ধর্ম আসলেই হুমকির মধ্যে ছিল, বিশেষ করে ইহুদী এবং রোমান শাসকদের পক্ষ থেকে। St. Paul এবং St. Peter- এই দুজন সচেতনভাবে চেষ্টা করছিলেন যে, খ্রিষ্ট ধর্মকে বনু ইসরাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার বিষয়টি কীভাবে ভাঙা যায়। তখন St. Peter দাবি করলেন যে, যীশু খ্রিষ্ট তাকে স্বপ্নযোগে দৈববাণী দিয়েছেন: “আমার বাণী নিয়ে ছড়িয়ে পড়ো।”
এরপর এই বিষয়টি নিয়ে খ্রিষ্টানদের মধ্যে বহু বিতর্ক হয়। ‘আদৌ খ্রিষ্ট ধর্ম বনু ইসরাইলের বাইরে প্রচার করা যাবে কিনা?’- এই নিয়ে তাদের ধর্মসভা হলো এবং সেখানেও St. Peter কখনো বলেননি যে, যীশু খ্রিষ্ট তাকে জীবিত অবস্থায় আদেশ দিয়েছেন। তার মানে হচ্ছে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের ব্যাপারটি যীশু খ্রিষ্টের পক্ষ থেকে আসেনি।
পরবর্তীকালে এই নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতি অর্থাৎ প্রচারের মাধ্যমে ধর্ম ছড়াতে হবে- এই প্রক্রিয়া বিস্তৃত হতে থাকলো। তখনও কিন্তু খ্রিষ্টানদের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ এই বিস্তারের পক্ষে ছিল না। তারা এই বিতর্ক জারি রেখেছে এবং কয়েক শতাব্দী ধরে তা চলমান ছিল। শেষ পর্যন্ত যারা প্রচারণায় বিশ্বাসী ছিল, তারা জয়ী হয়ে গেল এবং বনু ইসরাইলের বাইরে থেকে Emperor Constantine খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে এর প্রধান অভিভাবক হয়ে উঠলেন।
খ্রিষ্টীয় সভ্যতা এবং পুরো মানবজাতির ইতিহাসে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সালেই স্পেনে মুসলমানদের দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটেছে, অপরদিকে Christopher Columbus অ্যামেরিকায় উপনীত হয়েছেন, যার মাধ্যমে নতুন দুটি মহাদেশ খ্রিষ্টীয় সভ্যতার অধীনে আসার পথ উন্মোচিত হয়েছে। একইসাথে ইউরোপে নৌ-বিপ্লবের নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। Columbus-এর ব্যক্তিগত সহকারী Dr. Chanca সরাসরি লিখেছেন যে, Queen Isabella এবং King Ferdinand এর কাছে Columbus চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে তিনি বলেছেন যে, “এই অভিযান ‘Saracen’-দের বিরুদ্ধে।” ‘Saracen’ মানে ‘শয়তানের বাহিনী’ যা দ্বারা তারা মুসলিমদেরকে বোঝাতো। এই অভিযানের মধ্য দিয়ে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করতে চান, জেরুজালেম দখল করতে চান। অর্থাৎ, আগের Crusade-গুলো হয়েছে স্থল পথে; তখন সর্বশক্তি ব্যয় করেও তারা জয়ী হতে পারেনি। এখন তারা ভাবছে যে, নৌ পথে ভিন্ন রাস্তা ধরে যদি তারা প্রাচ্যের অঞ্চলে উপনীত হতে পারে বা ফিলিস্তিনে পৌঁছতে পারে, তাহলে সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে তারা সাফল্য অর্জন করবে।
এই নৌ অভিযান সমূহের মধ্য দিয়ে স্পেন এবং পর্তুগাল কেবলমাত্র ক্রুসেডীয় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে চাইছিল তা নয়, বরং তারা বাণিজ্যিক বিস্তারও লাভ করতে চাচ্ছিল। তখন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ স্বর্ণের সন্ধানে অভিযান করত। স্পেন এবং পর্তুগালের মধ্যেও আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্ব তৈরি হল। এই দ্বন্দ্ব নিরসনে ভূমিকা রাখলেন Pope Alexander (VI) ।
তিনি পোপ হিসেবে দায়িত্বপালনকালে (১৪৯২-১৫০৩) যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে একটি হলো The Treaty of Tordesillas। এই চুক্তি স্পেন এবং পর্তুগালের মধ্যে হয়, যার মাধ্যমে তিনি ইউরোপের বাইরে গোটা পৃথিবীকে স্পেন এবং পর্তুগালের মধ্যে ভাগ করে দেন; পশ্চিমভাগ দেন স্পেনকে আর পূর্বভাগ দেন পর্তুগালকে; উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ দখল করে শাসন করবে স্পেন আর আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপসমূহ, মালাক্কা দ্বীপসমূহ দখল করে শাসন করবে পর্তুগাল। সেই অঞ্চলসমূহের মানুষ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সম্পদ- সমস্ত কিছুর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং অত্যাচার-নিপীড়ন করা, শোষণের কাঁচামাল হিসেবে এসব মানুষদের ব্যবহার করা- এইসব তাদের জন্য বৈধ, শর্ত হচ্ছে: সেই সমস্ত এলাকায় বসবাসকারী ‘অসভ্য’ মানুষদের খ্রিষ্ট ধর্মের শিক্ষা দিতে হবে। এভাবে ঔপনিবেশিকতার চাবি স্প্যানিশ এবং পর্তুগিজদের হাতে চলে আসল।
ফলস্বরূপ আমরা দেখি যে, পর্তুগিজ নাবিক Vasco Da Gama ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মে মাসের ২০ তারিখ কালিকটবন্দরে উপনীত হয়ে সেখানে কী নির্মম গণহত্যা চালিয়েছেন! কী নিষ্ঠুরতা চালিয়েছেন! অক্ষয়কুমার মৈত্রের ‘ফিরিঙ্গি বণিক’ নামক বইয়ে তার বর্ণনা আছে। তৎকালীন ল্যাটিন, পর্তুগিজ, আরবি গ্রন্থাবলীর মধ্যেও তার বিবরণী পাওয়া যায়। সব নিষ্ঠুরতা বৈধ, কারণ তিনি একটি ‘পবিত্র’ অভিযানে বেড়িয়েছেন। তিনি যখন অভিযানে বের হবেন, তখন ইউরোপীয়রা সমুদ্রে বের হতে ভয় পাচ্ছিল। তাই যারা খুনের কারণে কারাবন্দী বা চিহ্নিত-দাগি আসামি- এই শ্রেণির মানুষদের, যারা জীবনের আশা হারিয়ে ফেলেছে এবং জীবনে আর হারাবার কোনো কিছু নেই, জাহাজে করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তারপর থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে অব্যাহতভাবে ডেনিশ, ফরাসি, ব্রিটিশ, ওলন্দাজ- সবাই এসেছে। শুধু ভারত নয়, বরং ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া- পৃথিবীর চতুর্দিকে তারা ছড়িয়ে পড়েছে।
সকল ঐতিহাসিক এটি স্বীকার করবেন যে, এই ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম লক্ষ্যগুলোর মধ্যে একটি ছিল খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচার। আমরা দেখি যে, ভারতে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রধান ধারাসমূহ অনবরত এসেছে, একের পর এক। একটি বর্ণনা প্রচলিত আছে, যদিও এর কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, যে, St. Thomas the Apostle প্রথম খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচারক, যিনি ৫০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন এবং ৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মালাবার উপকূলে ধর্ম প্রচার করেছেন।
কিন্তু ঐতিহাসিক বিবরণ খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচারের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আমাদেরকে যে তথ্য দেয়, সেখানে আমরা দেখছি যে, ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে Antonio Vaz এবং Pedro Dias ভারতে আগমন করলেন খ্রিষ্ট ধর্মের Catholic ধারা প্রচার করতে। ১৫৮০ খিষ্টাব্দে Roman Catholic ধর্মযাজকদের একটি দল ভারতে আগমন করেন। ওলন্দাজদের তৈরি Bandel শহরকে তারা নিজেদের কর্মস্থলে পরিণত করেন। শুরুর দিকে আগমনকারী এসকল ধর্মপ্রচারক ছিলেন Jesuit Christian এবং Roman Catholic। ১৫৯৯ সালে তারা নিজেদের গির্জা, মঠ এবং স্কুল ইত্যাদি স্থাপন করেন।
এই ধারাবাহিকতায় দেখা যায় যে, ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান এক ফরমানের মাধ্যমে গির্জার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। এসব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অন্যতম হলো: ৭৭৭ একর নিষ্কর জমি প্রদান। অর্থাৎ, ততদিনে গির্জা একজন সম্রাটের মনোযোগ লাভের সক্ষমতা তৈরি করে ফেলেছে। এই সুবিধা পরবর্তীতে ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা-ই বাতিল করে দেয়, কারণ তারা মনে করেছিল যে, খ্রিষ্টান মিশনারিরা এ অঞ্চলে বেশি সক্রিয় হলে স্থানীয় মুসলমানেরা তাদের ধর্ম বিপন্ন হচ্ছে- এই ভেবে বিদ্রোহ করে বসতে পারে।
এরপর Protestant ধর্মযাজকদের দল এখানে আসেন। ব্রিটেনে তখনও Reformation Movement চলমান। এই সময়ে অনেকগুলো Missionary Society তৈরি হয়, যাদের প্রতিষ্ঠাকাল খুব নিকটবর্তী। ১৭৯২ সালে Baptist Missionary Society, ১৭৯৫ সালে Church Missionary Society এবং ১৭৯৯ সালে London Missionary Society প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সমস্ত অঞ্চলে ব্রিটিশরা গিয়েছে, সে সমস্ত অঞ্চলে এসব সংগঠন তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে Protestant মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছে।
তারপর আগমন ঘটে Evangelical Christian-দের। Alexander Duff (১৮০৬-১৮৭৮) এর অধীনে বাংলায় ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে Evangelical Church প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি একাধারে পণ্ডিত, প্রাচ্যবিদ, রাজনীতিবিদ, বহু ভাষাবিদ ছিলেন। এই তিন মতবাদ তখন চরম সংঘাতে লিপ্ত ছিল। ইউরোপে Catholic ও Protestant এবং ব্রিটেন-স্কটল্যান্ডে Protestant ও Evangelical-দের মধ্যে তীব্র সংঘাত চলমান, অনেকটা আমাদের সুন্নি ও শিয়াদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মতো।
এই পরিস্থিতিতে ভারতেও তাদের সংঘাতে লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখানে তারা ধর্ম প্রচারের স্বার্থে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে নেয়। তারা ঠিক করে নেয় যে, তাদের একজনের এলাকায় অন্যজন নিজ মতবাদ প্রচার করতে যাবে না। একইসাথে তাদের ধর্মীয় বিতর্কগুলোকেও তারা জনসম্মুখে না আনার সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ, বিতর্ক গুলো পণ্ডিত পরিসরে থাকবে, তবে তারা একে জনসাধারণের পরিসরে নিয়ে আসবেনা।
খ্রিষ্টান মিশনারি কার্যক্রমের বিপ্লবার্থক পরিবর্তন আসে William Carey-র হাত ধরে। তিনি Baptist Missionary Society -এর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন। তার জীবনে অনেক উত্থান-পতন রয়েছে। গির্জা তাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করেছে, তার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছে। তখন এই ধরনের ঘটনা খুব স্বাভাবিক ছিল। ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনকারীদের মধ্যে নতুন যে প্রজন্ম, তারা নিজেদেরকে বিশ্বজয়ী ভাবতো এবং সেই মানের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তারা সবসময় উদগ্রীব থাকতো।
তার মতোই আরো একজন হচ্ছেন William Jones। তিনি তরুণ বয়সে ইউরোপে থাকতেই আরবি শিখেছেন। তিনি কলকাতায় এলেন বিচারক হিসেবে। এসে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে The Asiatic Society প্রতিষ্ঠা করেন। তার মধ্যে একটি বৈশ্বিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার প্রস্তুতি কৈশোর থেকেই ছিল। তার জীবনে Carey-র জীবনের মতো এত উত্থান-পতন নেই। তিনি একইমাত্রার আকাঙ্কা নিয়ে ভারতে আসেন যে, ধর্ম প্রচার করতে হবে, ধর্মের বাণীকে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং ‘বর্বর-নিকৃষ্ট’ এই মানুষগুলোকে সভ্য করে তুলতে হবে।
তিনি ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে Baptist মতাদর্শের ওপর Serampore Mission প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামপুর তখন Danish East India Company-র নিয়ন্ত্রণে ছিল। তার প্রধান সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন Joshua Marshman (১৭৬৮-১৮৩৭) এবং William Ward (১৭৬৯-১৮২৩)। Carey এবং তার দুই বন্ধুর হাত ধরে ভারত উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলায় কলকাতা কেন্দ্রিক বড় ধরনের এক পরিবর্তন হয় (কারণ তখন বাংলার রাজধানী ছিল কলকাতা)।
Serampore Mission এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, সেই সময়ে তারা সেখানে নিজস্ব প্রেস তৈরি করে বাংলা, অহমিয়া, উরিয়া, হিন্দি, মারাঠি, সংস্কৃত এবং আরো নানা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেছে। বাইবেলের অনুবাদ ছাড়াও তারা ভারতীয় সহযোগীদের দিয়ে (যেমন: রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার) রামায়ণ, গীতা ও অন্যান্য পুরাণের ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে Dominant বানিয়েছে।
এই পরিবর্তনের দুটি ধারা: একটি ছিল Asiatic Society ভিত্তিক, আর অপরটি ছিল Fort William College ভিত্তিক। Asiatic Society প্রাচ্যবিদ্যা নিয়ে কাজ করেছে আর Fort William College-ও তার সাথেই সমান্তরালভাবে কাজ করেছে। এক প্রতিষ্ঠান আরেক প্রতিষ্ঠানের অসম্পূর্ণতা, দুর্বলতা, ত্রুটি- এগুলো দূর করার চেষ্টা করেছে। Asiatic Society প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ জন্য যে, ভারতের মানুষদের শাসন করতে হলে তাদেরকে জানতে হবে, অন্যথায় তাদের ওপর সাময়িক শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে বটে, কিন্তু পরবর্তীতে তা একটি দুর্ঘটনা হিসেবে ইতিহাসের অতলে হারিয়ে যাবে।
১৭৮৪ থেকে নিয়ে ১৮২৮ পর্যন্ত Asiatic Society-তে স্থানীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, হোক সে মুসলিম অথবা হিন্দু। ইংরেজরা মনে করতো যে, এটি একটি Elite প্রতিষ্ঠান। তারা কী চিন্তা করে বা জ্ঞানচর্চা করে- এটি যদি এই স্থানীয়রা জেনে যায় তাহলে হয় তারা কিছু বুঝবে না অথবা বুঝবে এবং তাহলে এটি তাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, কারণ স্থানীয়দের আনুগত্য তখনো পরীক্ষিত নয়।
স্থানীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম Asiatic Society-তে প্রবেশাধিকার পেলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনি ইংরেজি ক্লাবের সদস্য হন এবং কলকাতায় প্রথম Union Bank প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে তিনি তাদের বিশ্বাসভাজন হলেন। তার কাছাকাছি সময়ে স্থানীয়দের আরো অনেকে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন। যেমন: রাজেন্দ্রলাল মিত্র; তিনি লাইব্রেরিয়ান ও গবেষণা সহকারী ছিলেন, তারপর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অতঃপর ১৮৮৫ সালে তিনি Asiatic Society-র সভাপতি হন।
এই প্রতিষ্ঠান অনেক বড় বড় পন্ডিত তৈরি করেছে, যেমন: Charles Wilkins, Henry T. Colebrooke, Alexander Cunningham। এরা সবাই Orientalist বা প্রাচ্যবিদ ছিলেন। এই প্রাচ্যবিদ্যা আমাদের সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম ও তা আমাদের জীবনে কীভাবে প্রতিফলিত হয়, কৃষি, সমাজব্যবস্থা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, পারস্পরিক বন্ধন এবং মনস্তত্ত্ব- এই সমস্ত কিছুকে অধ্যয়ন করেছে। এই অধ্যয়ন খ্রিষ্টান মিশনারিদের সহায়তা করেছে। আবার, খ্রিষ্টান মিশনারিদের ধর্মীয় তৎপরতা Asiatic Society-র ভাবাদর্শকে সহায়তা করেছে।
British East India Company-র যিনি প্রধান থাকতেন, তিনি এই Asiatic Society-র প্রধান পৃষ্ঠপোষক হতেন। যেমন: এর প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তৎকালীন কোম্পানি-প্রধান Warren Hastings। এখানে Asiatic Society-র কয়েকটা বিষয় লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা; দ্বিতীয়ত, গবেষণা প্রতিষ্ঠান; তৃতীয়ত, ধর্মপ্রচারক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা; চতুর্থত, অর্থায়ন, যা East India Company বিপুল মাত্রায় করেছে। এভাবে সবকিছুর এক অসাধারণ সমন্বয় তারা সেখানে নিশ্চিত করেছিল।
William Carey এবং তার সহযোগীরা দেশীয় ভাষা এবং সাহিত্যের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ ভাষা এবং সাহিত্য আধিপত্য বিস্তারের এমন এক জায়গা যার ওপর আধিপত্য সহজে শেষ হয় না। কোনো এক সময় যদি প্রত্যক্ষ উপনিবেশ হারিয়েও যায়, তাহলেও মস্তিষ্কের উপনিবেশ, ভাষাগত উপনিবেশ এবং সাংস্কৃতিক উপনিবেশ হারাবে না।
Asiatic Society-তে সকল ধারার পণ্ডিত ছিলেন, যেমন: ভাষাতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ , ধর্মতাত্ত্বিক ইত্যাদি। এমনকি সেখানে যারা মর্মী সাধনা করতেন, তারাও ছিলেন। এদের কেউ ছিল হিন্দু ধর্মের প্রতি অনুরক্ত, কেউ মুসলিম বিষয়াবলির প্রতি অনুরক্ত, কেউ আরবি ভাষার প্রতি অনুরক্ত, কেউ ফারসির প্রতি অনুরক্ত। এই অনুরাগ ছিল লিপ্ততার অনুরাগ। তারা এগুলো নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সেরা গ্রন্থসমূহ, যেমন: ‘তাবাকাতে নাসেরি,’ ‘তারিখ-ই-ফিরোজ শাহ,’ ‘তারিখ-ই-ফিরিশতা,’ ‘তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী,’ ‘ফতোয়া আলমগীরী’- এইসকল গ্রন্থ তারা অনুবাদ করেছে।
একইভাবে বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত ব্যকরণ গ্রন্থ লিখেছেন Nathaniel Halhed। বাংলা এবং লাতিন অভিধান তৈরি করেছেন Manual da Assumpção। এমনকি ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে উপমহাদেশের প্রথম বাংলা পত্রিকা ‘সমাচার দর্পণ’ সম্পাদনা করেন William Carey। বাংলা ভাষায় কথ্যরীতির প্রথম নিদর্শন হিসাব বিবেচনা করা হয় তার কাজগুলোকে। এদের কেউই বাংলা ভাষার সেবা করার জন্য আসেননি। খ্রিষ্ট ধর্মপ্রচারের জন্য তারা ভাষার ওপর এত ভূমিকা রেখেছেন! কারণ, এ অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের জন্য স্থানীয় ভাষা জানতে হবে। আর যেহেতু বিদেশিরা এই ভাষা শিখবে, সেহেতু তাদের জন্য এই ভাষার সুসংগঠিত ব্যকরণ গ্রন্থ থাকা লাগবে। এসব কারণেই তারা বাংলা ভাষার ওপর এতো ভূমিকা রেখেছেন এবং এগুলোর ভিত্তিতে তারা নতুনভাবে ভারতের পরবর্তী জ্ঞানব্যবস্থাকে সাজিয়েছেন।
আমরা ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে এখনো উচ্চমার্গীয় যেসমস্ত স্তরের কথা ভাবছিও না, তারা কিন্তু সেই কাজগুলো করার মধ্য দিয়েই এখানে আমাদের ওপর Monopoly (একচ্ছত্রতা) এবং Hegemony বা বুদ্ধিবৃত্তিক একচ্ছত্রতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এগুলো অলৌকিক কোনো ব্যাপার নয় যে, এমনি এমনি হয়ে গেছে; আর না এটি কোনো ষড়যন্ত্রতত্ত্ব। এটি সাধনা এবং আত্মনিয়োগের এমন এক সিলসিলা (ধারাবাহিকতা), যদি আমরা এমন করতাম, তবে ইউরোপীয়রাও আমাদের বশ্যতা স্বীকার করত এবং আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়ার জন্য নিজেদের চিন্তা, বিবেক ও মানসিকতাকে প্রস্তুত করত।
প্রথমে ইংরেজরা এসেছিল বাণিজ্যের মাধ্যমে, তারপর আমাদের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজনীতি, সামরিক শক্তি এবং কূটনীতি- সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে তারা আমাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল। এই কর্তৃত্ব ভঙ্গুর হতে পারত, না টিকতে পারত; কিন্তু এই কর্তৃত্ব যেন স্থায়ী হয় এবং আমরা যেন শাসিত হওয়ার ওপর সন্তুষ্ট থাকি- এই পথরেখা তৈরি করে দিয়েছিল তাদের পরবর্তী গবেষক এবং চিন্তাবিদগণ।
তৎকালীন আফ্রিকা, ল্যাটিন অ্যামেরিকা, ভারত ইত্যাদি যত জায়গায় উপনিবেশ ছিল, সেসবের মধ্যে তারা এক ধরনের আন্তঃসম্পর্ক তৈরি করেছিল। অর্থাৎ, যিনি আগে ভারতে কাজ করেছেন, তাকে পাঠানো হতো ভারতে। আবার, যিনি মধ্য এশিয়ায় কাজ করেছেন, তাকে পাঠানো হতো আরেক জায়গায়। এভাবে তারা এক ধরনের আন্তঃঔপনিবেশিক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল।
উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সুইজারল্যান্ডে Basel Missionary Seminary প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে তারা ধর্মীয় অধ্যয়নের জন্য ইবনে হাজম আন্দালুসী-র গ্রন্থাবলী, ইবনে তাইমিয়া-র ‘আল-জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালাদ দীনাল মাসিহ’, মুহাম্মাদ আল-শাহরাস্তানী-র ‘কিতাব আল-মিলাল ওয়াল-নিহাল’, আবুল হাসান আলী আল-মাসউদী রচিত ‘মুরূজ আয-যাহাব ওয়া মা’আদানিল জাওহার’, আল-বিরূনী-র গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করত। এমনকি ইবনে হাজমকে তারা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ‘Father’ হিসেবে উল্লেখ করত। এর পাশাপাশি কুরআন, হাদিস এবং মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত ভাষাসমূহ, যেমন: আরবি, ফারসি, তুর্কি, উর্দু ইত্যাদি ভাষা তারা এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করত।
এই Basel Missionary Seminary-তে Karl Gottlieb Pfander শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে আরবি, ফারসি ভাষা জানতেন। প্রথমে তাকে পাঠানো হয় রাশিয়ায়। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জার্মান ভাষায় ‘Waage der Wahrheit’ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে রূশ সরকার রাশিয়ায় জর্জিয়া মিশনারিদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়, কারণ সেখানে খ্রিষ্টান মিশনারিগণ সমাজের ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ইত্যাদির বিরুদ্ধাচরণ করে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তারপর তিনি বাসেল এ ফিরে যান এবং সেখান থেকে তাকে বিশেষভাবে ভারতে পাঠানো হয়। তিনি উর্দু ও ফারসি ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ, যেমন: ‘মিফতাহুল আসরার’(রহস্যের চাবি), ‘তরিকুল হায়াত’(জীবনের পথ) ইত্যাদি রচনা করেন এবং তার ‘Waage der Wahrheit’ গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ ‘মিজানুল হক’ প্রকাশ করেন।
ভারতে Pfander তার ইসলামবিরোধী কার্যক্রম জোরালোভাবে চালাতে থাকেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, দিল্লি জামে মসজিদের সামনে গিয়ে তিনি মুসলিম পন্ডিতদের উদ্দেশ্যে হুংকার ছুড়েন যে, কে আছে আমার সাথে বিতর্ক করবে? ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সত্যতা প্রমাণ করবে? উপমহাদেশের সমস্ত মানুষদের ধর্মীয় জীবন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হতো, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে-দেয়ালে মিশনারিদের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। তারা চায় যে, কেউ বেরিয়ে আসে তাদের জবাব দিক। তারপর মুসলিমদের তরফ থেকে প্রতিক্রিয়া আসতে থাকল।
তৎকালীন ইসলামী জ্ঞানচর্চার অন্যতম দিক ছিল তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হলো: এক খ্রিষ্টান পাদরি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী-র পরিবারের কারো সাথে বিতর্ক করতে চাইলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, যদি এই পরিবারের কাউকে তিনি বিতর্কে পরাজিত করতে পারেন, তাহলে সমগ্র দিল্লি তার কাছে পরাজিত হবে। তাই, তিনি দেহলভী পরিবারের সবচেয়ে কম বাকপটু ব্যক্তি, আব্দুল কাদির মুহাদ্দিস দেহলভী-র সাথে বিতর্ক করতে চাইলেন। এরপর বিতর্কের সময় আব্দুল কাদির মুহাদ্দিস দেহলভী তাকে বললেন যে, আপনি এই এই বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন, তাই তো? তখন সেই খ্রিষ্টান পাদরি হতভম্ব হয়ে গেলেন, কারণ, তিনি যেসব প্রশ্ন নিয়ে এসেছিলেন, তার সবই তিনি তুলে ধরেছেন। তাহলে এসবের জবাব-ও তো নিশ্চয় তার কাছে হাজির আছে।
তখন আব্দুল কাদির মুহাদ্দিস দেহলভী বললেন যে, শুনুন, আপনি পরীক্ষার জন্য এমন জায়গায় এসেছেন, যা আপনার উচিত হয়নি। আমরা কুরআনের তাফসীর পড়ার আগে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করি। যখন আমরা কুরআনের তরজমা পাঠ করে ফেলি, তারপর আমরা তাওরাত, যাবূর, ইনজিল এবং এদের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো পড়ে ফেলি। আশরাফ আলী থানবী রহিমাহুল্লাহ-র গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।
অন্যান্য মনীষীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জাওয়াদ সাবাত আল হুসাইনী। তাকে জাহাজডুবির নামে খ্রিষ্টান মিশনারিরা হত্যা করে ফেলেছিল। তাঁর রচনাসমূহের ধারাবাহিকতা পরবর্তীতে আরেক মহান মুসলিম মনীষী রহমাতুল্লাহ কিরানবী-কে প্রস্তুত করে।
মুজাফফরনগরের কিরানা-র অত্যন্ত অভিজাত ডাক্তার পরিবারে রহমাতুল্লাহ কিরানবী-র জন্ম। তাঁর পরিবার সম্রাট আকবরের আমল থেকেই মুঘল সালতানাতের সাথে যুক্ত ছিল। আবার, জ্ঞান চর্চার ধারাও সেই পরিবারে ছিল। তিনি ৬ বছর বয়সে ইসলামী শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী ধারায় যুক্ত হন, ১২ বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করেন, আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষা শিখেন। তারপর দিল্লিতে গিয়ে দর্শন, গণিত এবং চিকিৎসা শিখেন।
রহমাতুল্লাহ কিরানবীর বংশের আরেকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন ডাক্তার উজির খান। তিনি বিহারে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাংলার মুর্শিদাবাদে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও কলকাতা মেডিকেল কলেজ হতে চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন করেন। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি দেখতে পেলেন যে, মিশনারি কার্যক্রম ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। তারপর তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যান। সেখানে খ্রিষ্ট ধর্মকে সমালোচনা করার জন্য গ্রিক, লাতিন এবং ইংরেজি ভাষার ওপর দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি খ্রিষ্ট ধর্মের ওপর তৎকালীন গবেষকদের মূল্যবান গ্রন্থাবলী বিপুল মাত্রায় সংগ্রহ করে ভারতে ফিরে আসেন। ইংরেজরা আমাদের সংস্কৃতিকে জানার জন্য ইউরোপীয় হয়ে আমাদের ভাষা শিখেছিল। আর আমাদের সবচেয়ে অগ্রসর, সোনালি সন্তান, তিনি তাদের মোকাবেলা করতে তাদের ভাষাগুলো শিখেন, তাদের গ্রন্থসমূহের ওপর গভীর সমালোচনামূলক এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা অর্জন করেন।
তিনি দেশে এসে দেখেন যে, রহমাতুল্লাহ কিরানবী-র সাথে পাদরি Pfander-এর চিঠি আদান-প্রদান হচ্ছে। কিরানবী-র যে জ্ঞান ছিল, তা মূলত ঐতিহ্যগত জ্ঞান। তখন, ডাক্তার উজির খান ইউরোপ থেকে অর্জিত সাম্প্রতিক বিষয়সমূহের জ্ঞান তাকে সরবরাহ করেন। ফলে রহমাতুল্লাহ কিরানবী-র জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ হয়। এভাবে তাঁরা একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হন।
১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ, সোমবার রহমাতুল্লাহ কিরানবী এবং Pfander এর মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের প্রথম বিষয় ছিল ‘নাসখ’ (রহিতকরণ); অর্থাৎ, ইসলামের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর বিধান রহিত হয়ে গেছে কিনা তা প্রমাণ করতে হবে। দ্বিতীয় বিষয় ছিল বাইবেলের বিকৃতি। তৃতীয় বিষয় ছিল Trinity (ত্রিত্ববাদ); বাইবেল এবং ইসলাম দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, Trinity গ্রহণযোগ্য নয়। চতুর্থ বিষয় ছিল ‘ইজাযুল কুরআন;’ অর্থাৎ, কুরআন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এবং কোনো মানুষ কুরআনের মতো কোনো কিছু রচনা করতে পারে না- তা প্রমাণ করা। সর্বশেষ বিষয় ছিল নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নবুয়তের প্রমাণ, এই পাঁচ বিষয়ে বিতর্ক হলো। বিতর্কে রহমাতুল্লাহ কিরানবী জয়ী হন এবং Pfander ভারত ছেড়ে ইস্তাম্বুলে পলায়ন করেন। পরবর্তীতে তাকে সেখান থেকেও পলায়ন করতে হয়েছিল। এই বিতর্কের বিষয়সমূহের ওপর ভিত্তি করে রহমাতুল্লাহ কিরানবী তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ ‘ইযহারুল হক’ রচনা করেন।
Pfander এর পরাজয় সাধারণ কোনো ব্যাপার ছিল না। ভারতের প্রান্তে-প্রান্তে, গ্রামে-গঞ্জে এর খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলমানেরা তখন শাসনক্ষমতা, অর্থনীতি, জমিদারি- সবকিছু হারিয়েছেন। রাষ্ট্রক্ষমতা খ্রিষ্টানদের হাতে থাকাকালীন জ্ঞান এবং প্রমাণের শক্তি দিয়ে খ্রিষ্টানদেরকে পরাজিত করার এই ঘটনা সমগ্র ভারতে, এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরেও বর্ষার পানির মতো ঈমানের প্রতি একটি চরম-চূড়ান্ত অঙ্গীকার এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।
আরো একজন মুসলিম মনীষী ছিলেন মুনশী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭)। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণকারী একজন দর্জি কীভাবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে শিক্ষা লাভ করে এখানে ধর্ম প্রচার করতে আসা বড় বড় খ্রিষ্টান প্রচারকদের মেরুদণ্ড কাঁপিয়ে দেবেন, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। তিনি হাতে হারিকেন নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-নগরে সর্বত্র একা প্রতিরোধে গড়ে তুলেন। তাঁর ক্ষমতা ও সামর্থ্য কী ছিল? তাঁর ক্ষমতা ছিল সেই জ্ঞান, যা রহমতুল্লাহ কিরানবী-কে শাসকদের বিপরীতে বিজয় দান করে। যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যেত না, যেই সাম্রাজ্যের প্রধান লক্ষ্যসমূহের একটি ছিল ধর্মপ্রচার, সেই ধর্মপ্রচারের সমগ্র প্রচেষ্টাকে তিনি প্রকাশ্যে পরাজিত করেন।
তিনি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মীয় প্রেরণার বিস্তার ঘটানোর জন্য ‘ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা’ নামে একটি সংস্থা তৈরি করেন। কলকাতায় তিনি ‘সুধাকর’ ও ‘ইসলাম প্রচারক’ পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করতেন। ধর্ম, সমাজকল্যাণ এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গ্রন্থসমূহ অত্যন্ত মূল্যবান। যেমন:‘খ্রিষ্টীয় ধর্মের অসাড়তা’ (১৮৮৭), ‘বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদভান্ডার’ (১৮৯৪), ‘মেহেরুল ইসলাম’ (১৮৯৭), ‘হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা’ (১৮৯৮), ‘মুসলমান ও খ্রিষ্টান তর্কযুদ্ধ’ (১৯০৮)। এছাড়াও তিনি অসংখ্য বিতর্কে খ্রিষ্টানদের পরাজিত করেছেন।
আল্লাহ তায়ালা তাকে অসামান্য দক্ষতা, বাগ্মিতা, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা এবং প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন। যেমনভাবে তাঁর কলম সক্রিয় ছিল, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, ঠিক তেমনি তাঁর জবানও ছিল সক্রিয়। তিনি বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে বেরিয়েছেন দ্বীনের বার্তা নিয়ে। একইসাথে সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি- সমস্ত কিছুর ওপর তাঁর তীক্ষ্ণ এবং ধারালো অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তিনি যে কেবল নিজে ধর্ম প্রচার করেছেন তা নয়, বরং বহু প্রচারক ও লেখক তৈরি করেছেন।
তাঁর শাগরিদদের অন্যতম একজন হলেন শেখ জমিরুদ্দীন। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদ St. Paul’s Divinity College থেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ওপর স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর কলকাতার Divinity College থেকে আরও উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন। খ্রিষ্ট ধর্মতত্ত্ব, ইংরেজি, লাতিন, সংস্কৃত, আরবি, গ্রিক, হিব্রু ভাষা এবং এই সমস্ত ভাষাসাহিত্য, ব্যকরণ ইত্যাদির ওপর তার ছিল অগাধ দখল। তিনি খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে নেন এবং ‘জন জমিরুদ্দীন’ নাম গ্রহণ করেন। ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে ‘খ্রিষ্টীয় বান্ধব পত্রিকা’-য় তিনি কলাম লিখেন যে, ‘আসল কোরান কোথায়?’
এই চ্যালেঞ্জের জবাবে দাঁড়িয়ে যান মুনশী মেহেরুল্লাহ। তিনি ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসের ২০ তারিখে ‘সুধাকর’ পত্রিকায় কলাম লিখেন: “ইশায়ী বা খ্রিস্টানী ধোঁকা ভঞ্জন” ; আবার, ২৭ তারিখে লিখেন: “আসল কোরান সর্বত্র।” এ বিতর্কের মধ্যে জন জমিরুদ্দীন পরাস্ত হন এবং মুনশী মেহেরুল্লাহর হাতে পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।
আমরা আরো দেখব যে, William Muir ১৮৫০ সালে ‘The Life of Mahomet’ নামে দুই খন্ডের বইয়ে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর জীবন নিয়ে অসংখ্য মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে অনেক আপত্তি উত্থাপন করে। এর জবাব দেন স্যার সৈয়দ আহমদ। এর জন্য পর্যাপ্ত গ্রন্থাবলী তাঁর কাছে ছিল না। তিনি নিজের জমি বিক্রি করে ব্রিটেন যান এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করে এর জবাব দেন। ফলে William Muir-কে তার গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে ভুলগুলো সংশোধন করতে হয়েছিল।
খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রাতিষ্ঠানিকতা, পৃষ্ঠপোষকতা এবং পদ্ধতিগত ধারাবাহিকতা ছিল। আর আমাদের মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং আত্মনিয়োগের মাধ্যমে এর মোকাবেলার ব্যাপারগুলো ঘটেছে। আমরা সেরকম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারিনি। তারপরও ঈমানের সুরক্ষা এবং দ্বীনি পরিচয়ের হেফাজতের জন্য অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান তৎকালীন কর্তৃত্বমূলক ভূমিকা পালন করেছে, যার মধ্যে অন্যতম দারুল উলুম দেওবন্দ।
এভাবে মুসলমানেরা অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি আমাদের ঐতিহ্যের ভেতর থেকে, আমাদের জ্ঞানব্যবস্থার ভেতর থেকে, আমাদের সামাজিক আত্মশক্তির ভেতর থেকে। আর এই ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হয়েছে আলেম এবং সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণির সমন্বয়ের মাধ্যমে।
সারাংশ:
১) বাইবেলে যীশু খ্রিষ্ট তাঁর ধর্মকে কেবল ইসরাইলিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ইসরাইলিদের বাইরে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার মূলত পরবর্তীদের উদ্ভাবন;
২) খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচারকাজ-ই মূলত ইউরোপীয়দের হাতে ঔপনিবেশিকতার চাবি তুলে দেয়;
৩) ইংরেজরা প্রাচ্যবিদ্যার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেছে, তাদের সংস্কৃতিকে অধ্যয়ন করেছে এবং এভাবে আমাদের মস্তিষ্কে উপনিবেশ স্থাপন করেছে;
৫) প্রত্যক্ষ উপনিবেশ না থাকলেও মস্তিষ্কের উপনিবেশ এখনো রয়ে গিয়েছে;
৬) খ্রিষ্টান মিশনারিদের অপপ্রচারের জবাব আমাদের পূর্বপুরুষগণ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দিয়েছেন, এমনকি এ উদ্দেশ্যে জ্ঞান আহরণে তাঁরা নিজেদের জায়গা-জমি বিক্রি করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। অতএব, আমাদেরও উচিত তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।


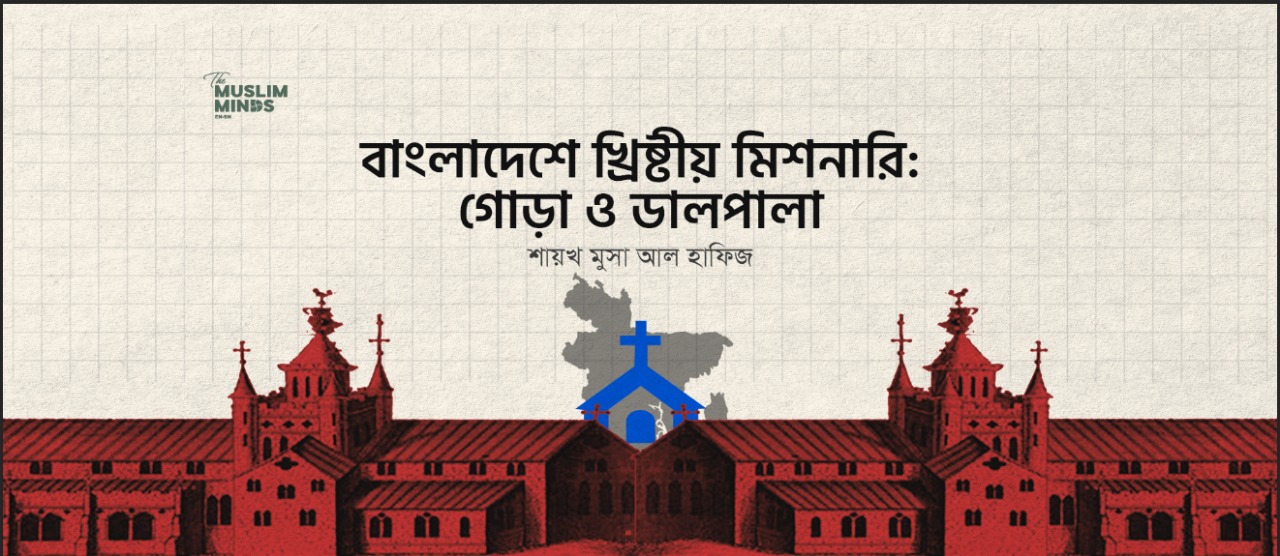

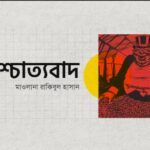
Leave a comment