আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় Occidentalism বা পাশ্চাত্যবাদ। পাশ্চাত্যবাদকে বোঝার প্রথমে আমাদের ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে। এর কারণ হলো, পাশ্চাত্যবাদ প্রাচ্যবাদের প্রতিক্রিয়া।
প্রাচ্যবাদ কী?
প্রাচ্যবাদ ধারণাটি নিয়ে এসেছেন এডওয়ার্ড সাইদ। তিনি ফিলিস্তিনের নাগরিক এবং একজন খ্রিষ্টান। জন্ম ১৯৩৫ সালে। নাকাবার সময় ফিলিস্তিন মুসলিমদের সাথে সাথে খ্রিষ্টানদেরকেও বাস্তুচুত্য করা হয়েছে। এডওয়ার্ড সাইদ বাস্তচ্যুত হয়ে প্রথমে মিশর এবং সেখান থেকে পরবর্তীতে আমেরিকায় পরিবার নিয়ে স্থায়ী হন। সেখানে তিনি শিক্ষকতা করতেন। আমেরিকায় থাকাকালীন তিনি একটি বিষয় খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করেন:
আরব হিসেবে তার যেই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা, তা পশ্চিমা মিডিয়ায় দেখানো দৃশ্যাবলির সাথে ব্যাপক পাথ্যর্ক।
তিনি দেখছেন যে, আরবা সেখানে নিপিড়িত, ইসরাইলিরা দখলদার। এর ফলে তার বাস্তুচুত্য হতে হয়েছে। আর মিডিয়ায় দেখছেন একেবারে বিপরীত চিত্র। তিনি মিডিয়ায় দেখছেন যে, ইসরাইলিরা নির্যাতিত, ফিলিস্তিনিরা তাদেরকে নিপীড়ন করছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন যে, আরব হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা আর মিডিয়ায় যেটা দেখছি তার মধ্যে দিনরাত পার্থক্য। এই পার্থক্যের কারণটা কী?
তখন তিনি বইপত্র সংগ্রহ করে পড়াশুনা শুরু করেন। সেখানে তিনি দেখেন যে, পশ্চিমের পরিব্রাজক বা স্কলাররা বিশেষ করে ১৮৫০ এর দশকের পর থেকে যেসমস্ত রচনাবলী রচিত হয়েছে সেখানে তারা পূর্ব বা প্রাচ্যকে একটা বিশেষ লেন্স দিয়ে দেখেছেন। সেই লেন্সটি হলো: পশ্চিম উঁচু, পূর্ব নিচু, পশ্চিম সভ্য, পূর্ব অসভ্য, পশ্চিম সাংস্কৃতিক, পূর্ব অসাংস্কৃতিক, পশ্চিম শিক্ষিত, পূর্ব অশিক্ষিত। এধরনের সাধারণ পার্থক্যের ভিতর দিয়ে তারা তাদের বইপত্র রচনা করেছেন। এর ফলে দুইটি ঘটনা ঘটেছে ঘটেছে।
- এই রচনার মাধ্যমে পূর্ব সম্পর্কে তাদের একটা চিন্তা গড়ে উঠেছে। যার মাধ্যমে তারা বুঝতে পেরেছে পূর্ব কেমন হতে পারে।
- কলোনিয়াল পিরিয়ড শুরু হওয়ার পর পশ্চিম যখন পূর্বে গেল, তারা দেখতে পেল তাদের যে, মাধ্যে যে কনসেপ্টগুলো ছিল সেগুলো বাস্তবতার সাথে মিলে না, সম্পূর্ণ আলাদা।
এই সময়ে দুইটি কাজ করার মতো ছিল-
- এতদিন ধরে তাদের যে চিন্তা ছিল, তা রিভার্স করা। বাস্তবতা যেহেতু দেখা যাচ্ছে ভিন্ন, তাহলে সেই অনুযায়ী চিন্তাটিকে রিফরমেশন করা।
- নিজেদের চিন্তার আলোকে এই পূর্বকে বিকৃত করার চেষ্টা করা। পূর্বের ভিতরেও সেই চিন্তাটা ঢুকিয়ে দেওয়া যেটা তারা করে। তারা পূর্বকে যেভাবে দেখে, পূর্বও যেন নিজেদের সেভাবে দেখে।
এই দুইটি কাজের মধ্যে তারা দুই নম্বরটাকেই বেছে নিয়েছে।
এর ফলে ওরিয়েন্টদের মাধ্যে আলাদা একটা ধারনা গড়ে উঠেছে, যেটা পশ্চিম তাদেরকে দিতে চাচ্ছে। আর বর্তমানে আমরা এই বিষয়টিই দেখতে পাই। আর এটা একটি প্রকল্পের মাধ্যেমে গাণিতিকভাবে প্রবেশ করানো হয়েছে। আর এই হচ্ছে “ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদ”।
সাইদ এখানে বলতে চাচ্ছেন যে, ভৌগলিক শাসনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিকভাবে প্রভাব বিস্তার করার যে প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদ।
এর ফলে সবচেয়ে বেশি যে কার্যকরী কাজটা হয়েছে তা হলো: পশ্চিমের কোনো ব্যক্তি যদি স্বাধীনভাবে বাস্তবতার আলোকে জানতে চায়, তাহলে এর কোনো উপায় নেই। কারণ, ওরিয়েন্টকে জানার জন্য যতগুলো মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যেতে হবে, তার সব জায়গায়ই ওরিয়েন্টাল থট বা চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত। কেউ যদি এর ভিতর দিয়ে যায়, তাহলে এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে তার চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটবে।
এডওয়ার্ড সাইদ সর্বপ্রথম এই বিষয়টাকে চিহ্নিত করেছেন যে, ওরিয়েন্টকে শাসন করা হচ্ছে একটি প্রকল্পের ভিতর দিয়ে। আর তিনি মিশেল ফুকোর দর্শনের মাধ্যমে ওরিয়েন্টালিজমকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এই দর্শনের ভিতর দিয়ে যারা যায় তাদের চিন্তা ও মানস দখলদারিত্বের প্রকোপে পড়ে যায়।
এটা হচ্ছে এডওয়ার্ড সাইদের ওরিয়েন্টালিজমের মূল তত্ত্ব। এখানে তিনি ওরিয়েন্টালিজমের ব্যসিক কিছু বিষয় নিয়ে এসেছেন যা অক্সিডান্টিলিজম বা পাশ্চাত্যবাদকে বুঝতে যা প্রয়োজনীয়। তারমধ্যে একটি হচ্ছে ‘সেল্ফ এন্ড আদার’। পশ্চিমরা নিজেদেরকে দেখে সেল্ফ হিসেবে, এর একটি ইমেজ তাদের মধ্যে আছে। আর সেই ইমেজটা হচ্ছে: আমরা যুক্তি দিয়ে কাজ করি। এর বাইরে যারা আছে তারা হচ্ছে ‘আদার, অপর বা অন্য’। অপরকে তারা যেই লেন্সের ভিতর দিয়ে দেখে, তা হলো ‘আদার’রা আবেগ দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়, যুক্তিবোধ নেই।
আদারকে আদারের মতো গড়ে তোলার বা চিত্রিত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় আদারিং বা আদারাইজেশন। অপরকে অপর হিসেবে গড়ে তোলা বা আমাকে অন্য থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করা। ওরিয়েন্টালিজমের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
এখানে ক্ষমতার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ওরিয়েন্টালিজমের মূল ধারণা হলো: পশ্চিমারা সামরিক দিক থেকে ক্ষমতাবান ছিল। তারা ওরিয়েন্ট শাসন করেছে, শাসনের সুবিধাার্থে অন্য অনুষঙ্গকে ব্যবহার করেছে। এই ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য জ্ঞান উৎপাদন করতে হবে। আর এই জ্ঞানের উৎপাদনই মূলত ওরিয়েন্টালিজমের দর্শন।
Occidentalism বা পাশ্চাত্যবাদ কী?
Occident ফরাসি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে পশ্চিম; ইউরোপের পশ্চিম অংশকে বলা হয় Occident বা পশ্চিম। আর Occidentalism বা পাশ্চাত্যবাদ মানে হলো: Occident বা পশ্চিমের বাইরের লোকেরা পশ্চিমকে যেভাবে দেখে। Orientalism বা প্রাচ্যবাদ মানে হলো হলো: পশ্চিমের লোকেরা পশ্চিমের বাইরের লোকদের কীভাবে দেখে।
Occidentalism এর একাডেমিক সংজ্ঞা বিভিন্ন মহলে বিভিন্নভাবে দেখা যায়। এর তিনটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে, এর ফলে সংজ্ঞার মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য দেখা যায়। একপক্ষের সংজ্ঞার সাথে আরেকপক্ষের সংজ্ঞার সাথে কোনো মিল পাওয়া যায় না।
দৃষ্টিভঙ্গি তিনটি হলো-
- হাসান হানাফি-র দৃষ্টিভঙ্গি।
- ইয়ান বুড়ুমা ও আভিশাই মারগালি’র দৃষ্টিভঙ্গি।
- পৃথিবীর কেন্দ্র পশ্চিম।
১.হাসান হানাফি-র দৃষ্টিভঙ্গি
প্রথম পাশ্চাত্যবাদ সম্পর্কে যিনি সর্বপ্রথম কথা বলেছেন, তিনি হলেন হাসান হানাফি। তিনি ১৯৯২ সালে মুকাদ্দিমা ফি ইলমিল ইস্তিগরাব নামে একটি বই প্রকাশ করেন। ইস্তিগরাব মানে হচ্ছে Occidentalism বা পাশ্চাত্যবাদ। তিনি সর্বপ্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এখানে তিনি প্রাথমিক ধারণা দিয়েছেন এবং তাত্ত্বিকদেরকে আহ্বান করেছেন যে, Orientalism বা প্রাচ্যবাদ যেমন একটি দর্শন; এর বিপরীতে পাশ্চাত্যবাদকেও একটি দর্শন হিসেবে কিভাবে দেখা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে।
তারপর তিনি ২০০৫ সালের দিকে আরো একটি বই প্রকাশ করেন, সেখানে তিনি একে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।
তার মতে পাশ্চাত্যবাদ বোঝার পূর্বে আমাদের এর উৎস সম্পর্কে জানতে হবে। এই ধারণাটি তিনি ফুকো থেকে নিয়েছেন। এডওয়ার্ড সাইদ যেমন ফুকো থেকে ধারণা নিয়েছেন, তেমন তিনিও ধারণা নিয়েছেন।
ফুকো যখন কোনো বিষয়কে বিশ্লেষণ করেন তখন তিনি দেখার চেষ্টা করেন, এই ডিসকোর্সটিতে কোন কোন উপাদানগুলো ভূমিকা রাখে। দেখা যায়, একটি ডিসকোর্স একটি পয়েন্ট থেকে প্রবাহিত না হয়ে একই সাথে অনেকগুলো জায়গা থেকে প্রবাহিত হয়। এই উপাদানগুলোকে তিনি নাম দিয়েছেন ফ্রন্টস। এখানে তিনি তিনটি ফ্রন্টস চিহ্নিত করেছেন।
- এখানে প্রথমে তিনি উল্লেখ করেছেন ‘সাপোর্টার অব ওল্ড হেরিটেজ’ (আরবি : তুরাস)। এখানে তিনি দুইটি শ্রেণিকে নিয়ে এসেছেন। এক. সালাফি বা যারা টেক্সচুয়াল ইসলামকে ফলো করতে চায়। দুই. ন্যাশনালিস্ট। এই দুই শ্রেণির মধ্যে একটা সাধারণ প্রবণতা আছে যে, আমাদের যে অতীত সেটা ছিল আমাদের সোনালী যুগ, আমাদের সেখানে ফিরে যেতে হবে। আমাদের গৌরবকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের অতীতে ফিরে যেতে হবে।
- পাশ্চাত্যবাদের যে দ্বিতীয় ধারাটি গড়ে উঠেছে তা হলো: লাভার অব দ্য ওয়েস্ট। অর্থাৎ, প্রাচ্যের যে অংশটি পশ্চিমকে সুপিরিয়র মনে করে। তারা মনে করে যে, আমাদের পশ্চিমের মতো হতে হবে।
- রিয়েলিস্ট অ্যাটেটিউট । এখানে তিনি পশ্চিম ও অপশ্চিম এর মধ্যে সমন্বয় করতে চেয়েছেন। এই শ্রেণির ক্ষেত্রে, অক্সিডেন্টের বাইরে যারা থাকে তারা নিজেদের ও পশ্চিমকে বিশ্লেষণ করে দেখে যে, অক্সিডেন্ট-এর কোন কোন বিষয়গুলো ভালো এবং কোন কোন বিষয়গুলো মন্দ, কোন বিষয়গুলো আমাদের জন্য প্রযোজ্য আর কোন বিষয়গুলো আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেগুলো আমাদের জন্য প্রযোজ্য তা আমরা গ্রহণ করব, বাকিগুলো বাদ দিবো।
এই তিনটি ফ্রন্ট হাসান হানাফির অক্সিডেন্টালিজমের ডিসকোর্স গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এই তিন ফ্রন্টের মাধ্যমে তার সারকথা হচ্ছে: অক্সিডেন্টালিজম হচ্ছে ওরিয়েন্টালিজমের রিভার্স। ওরিয়েন্টালিজমের মাধ্যমে অক্সিডেন্ট এতদিন একটি ইমেজ গড়ে তুলেছে। এখন ওরিয়েন্ট নিজেরাই অক্সিডেন্টালিজমের মাধ্যমে নিজেদের আলাদা একটি ইমেজ গড়ে তুলছে। অক্সিডেন্ট যেভাবে ওরিন্টালিজমের মাধ্যমে ‘সেল্ফ এবং আদার’ এর ধারণা গড়ে তুলেছে; ঠিক একইভাবে ওরিয়েন্ট, অক্সিডেন্টালিজমের মাধ্যমে ‘সেল্ফ এবং আদার’ এর ধারণা গড়ে তুলছে। তারা এভাবে নির্ণয় করছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা পশ্চিম থেকে আলাদা, কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের আলাদা থাকতে হবে।
কালচারাল দিকটি হাসান হানাফি খুব ভালোভাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ওরিয়েন্টালিজম আমাদের এমন একটি ধারণা দিয়েছে যে, দেয়ার ইজ ওয়ান এন্ড অনলি কালচার।
এর মাধ্যমে অক্সিডেন্ট বুঝাতে চায় পৃথিবীতে কালচার একটিই, তা হচ্ছে পশ্চিমা কালচার। বাকি যা আছে তা হচ্চে আনকালচার্ড। আর যদি কালচারাল হতে হলে পশ্চিমের এই একমাত্র কালচারকেই গ্রহণ করতে হবে।
কিন্তু হাসান হানাফি বলছেন: এখানে একক কালচার বলতে কিছু নেই। অনেকগুলো কালচার আছে, আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য সহ সব জায়গার কালচারই কালচার। পশ্চিমের কালচারও এরকমই একটি কালচার এবং এটির কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এভাবে তিনি অক্সিডেন্টালিজমকে ওরিয়েন্টালিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।
আরো একটি বিষয় তিনি খুব ভালোভাবে ফোকাস করেছেন, তা হলো: যদি পূর্ব নিজের অস্তিত্বকে ধরে রাখতে চায়, তাহলে তার কালচারকে টিকিয়ে রাখতে হবে। নিজের কালচার যদি টিকে থাকলে, তাহলে পূর্ব টিকে থাকবে আর এর মাধ্যমে পশ্চিমের আধিপত্য থেকে বের হয়ে আসতে পারবে।
এই অ্যাপ্রোচ থেকে যদি অক্সিডেন্টালিজমের সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহলে বলা যায়: Occidentalism is the study of West.
অর্থাৎ, অক্সিডেন্টালিজম হচ্ছে পশ্চিমকে অধ্যয়ন বা বিশ্লেষণ করা। এই বিশ্লেষণ হতে পারে অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি, একাডেমিক ক্ষেত্রে। এখানে তিনি সংজ্ঞাটি ব্যাপক রেখেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, যতভাবে ওয়েস্ট নিয়ে কথা বলা হয় তার সবই অক্সিডেন্টালিজমের অন্তর্ভুক্ত।
২.ইয়ান বুড়ুমা ও আভিশাই মারগালিট -এর দৃষ্টিভঙ্গি
অক্সিডেন্টালিজমের দ্বিতীয় অ্যাপ্রোচ গড়ে তুলেছেন ইয়ান বুড়ুমা নামে নেদারল্যান্ডের একজন তাত্ত্বিক ও লেখক। তার সাথে আছেন ইসরাইলি একজন তাত্ত্বিক ও দার্শনিক, আভিশাই মারগালিট।
এই দুইজন অক্সিডেন্টালিজমের আরেকটি ধারা গড়ে তুলেছেন। এই ধারাটির মূল কথা হচ্ছে: পশ্চিমের বাইরে সংস্কৃতিগুলো পশ্চিমকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে। সেই শত্রুভাবপন্নতা যেসব চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাই হচ্ছে অক্সিডেন্টালিজম।
Occident: The West in the Eyes of Its Enemies নামে ২০০৪ সালে প্রকাশিত বইয়ের মাধ্যমে তারা এই ধারণাটি তুলে ধরেন। এই ধারার অক্সিডেন্টালিজমের সূচনা ১৯৪২ সালে। ১৯৪২ সালে জাপান যখন আমেরিকার কাছে পরাজিত হয়, তখন জাপানের একদল বুদ্ধিজীবী কিয়োটো শহরে একত্রিত হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসেন। তারা এই প্রশ্নটি নিয়ে ভাবতে শুরু করেন যে, কীভাবে পশ্চিমকে মোকাবিলা করা যায় এবং কীভাবে জাপানের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও সমাজব্যবস্থাকে পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনের মুখে রক্ষা করা সম্ভব।
এই সম্মেলনকে ইয়ান বুড়ুমা এবং আভিশাই মারগালিত চিহ্নিত করেছেন ‘পশ্চিমের বিরুদ্ধে পূর্বের বিদ্রোহের সূচনা’ হিসেবে।
তারপর তারা একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। তাদের মতে Hatred against the West অর্থাৎ, পশ্চিমের বিরুদ্ধে ঘৃণা-ই হচ্ছে অক্সিডেন্টালিজম। আর এটিকে তারা এতই ব্যাপক মাত্রায় নিয়ে এসেছেন যে, তারা বলেন: মর্ডানিটির বিরুদ্ধে যারা আছে তারা প্রত্যেই অক্সিডেন্টাল। তারা বলছেন যে, অক্সিডেন্টালিজমের সূচনা হয়েছে পশ্চিমে হিটলারের মাধ্যমে আর পরবর্তীতে বাকিরা এটি অনুসরণ করেছে।
তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ত্রুটিপূর্ণ । তারা বলছেন যে, পশ্চিমের প্রতি ঘৃণা-ই হচ্ছে অক্সিডেন্টালিজম। আবার তারাই বলছেন যে, এর সূচনা খোদ পশ্চিমেই। এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে, পশ্চিম নিজেই নিজেকে ঘৃণা করে।
হাসান হানাফি বা অন্যরা এই বিষয়টিকে চিহ্নিত করেন যে, কেন তাদের মধ্যে এই বৈপরীত্য। তারা পূর্বের ব্যাপারে কী ধারণা রাখে তা এই পূর্বধারণার মাধ্যমে বের হয়ে আসে। তারা পূর্ব কে পশ্চিমের শত্রু হিসেবেও বিবেচনা করছে না। তাদের বিবেচনায়, পশ্চিমের শত্রু হওয়ার যোগ্যতা কেবলমাত্র পশ্চিমেরই আছে। পূর্ব যদি পশ্চিমের শত্রুও হতে চায়, তাহলে সেটাও পশ্চিমের অনুসরণের মাধ্যমেই হতে হবে।
৩.পৃথিবীর কেন্দ্র পশ্চিম।
এখানে ধরা হয় পশ্চিম পৃথিবীর কেন্দ্রে আছে এবং পূর্ব সেখানে যেতে চাচ্ছে; অর্থাৎ,Journey towards the Center বা কেন্দ্রের দিকে যাত্রা। । তো এই কেন্দ্রে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা কী?
পূর্ব যদি পশ্চিমের মতো নিজেদের পৃথিবীর কেন্দ্রে আসতে চায়, তাহলে তাকে পশ্চিমের কিছু মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে। আর এটিকে আন্তর্জাকিভাবে বলা হয় Core and Periphery। Core মানে হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র আর Periphery মানে হচ্ছে পৃথিবীর প্রান্তিক অঞ্চলগুলো। Periphery যদি Core এ যেতে চায়, তাহলে Core যেভাবে Core হয়ে উঠেছে সেগুলোকে আত্মস্থ করতে হবে।
এর সারকথা হচ্ছে যে, পশ্চিমের মূল্যবোধসমূহকে কীভাবে মূল্যায়ন ও আত্মস্থ করা হবে তা বিবেচনা করা। এটিই হচ্ছে অক্সিডেন্টালিজমের মূল কথা।
এই সংজ্ঞাটি হাসান হানাফির তৃতীয় ফ্রন্টের সাথে মিলে যায়: পশ্চিমের ভালোগুলোকে গ্রহণ করা আর মন্দগুলোকে বর্জন করা। কিন্তু এই ফ্রন্টে অনেক বৈপরীত্য পাওয়া যায়। এখানে অঞ্চল ভিত্তিক আলাদা আলাদা ধারা গড়ে উঠেছে। অনেক তাত্ত্বিক অনেক ভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। মোটাদাগে, পূর্ব কীভাবে সেন্টারে যেতে পারে সেটিই হচ্ছে অক্সিডেন্টালিজম।
উপহসংহারে যদি বলা হয় কোনটি বাস্তবের সবচেয়ে অনুকূল, তাহলে বলা যায়-
দ্বিতীয় যে অ্যাপ্রোচ যা শত্রুভাবাপন্নতার কথা বলে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ওরিয়েন্টালিজমের যেসব কনসেপ্ট আমরা দেখেছি সেখানে পাওয়ার ও নলেজ ছিল। অর্থাৎ, পশ্চিম উপরে ছিল, আর সেখান থেকে সে শাসন করত। আর শাসনের সুবিধার্থে সে কিছু জ্ঞান গড়ে তুলেছে। আর এই জ্ঞানের মাধ্যমে সে কিছু কালচার গড়ে তুলেছে। এতে সে তাদের চিন্তাধারাকে বিকৃত করে ফেলছে।
এখন অক্সিডেন্টালিজম যদি একইভাবে ওরিয়েন্টালিজমের মতো শত্রুভাবাপন্ন হতে হয়, তাহলে অক্সিডেন্টালিজমকে যারা প্রয়োগ করছে তাদের শাসনক্ষমতায় আসতে হবে, পশ্চিমকে শাসন করতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের চিন্তাধারাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করতে হবে, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। ওরিয়েন্টালিজমের হুবহু বিপরীতে অক্সিডেন্টালিজমকে দাঁড় করানো যাচ্ছে না।
হাসান হানাফি যা বলেছেন তা-ই হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেছেন, অপশ্চিমকে নিজের সম্পর্কে আত্মসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। এই গড়ে তোলা নিজেকে আধিপত্য বিস্তারকারীর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া নয়, বরং নিজেদের অস্তিত্ব টিকেয়ে রাখার স্বার্থে আত্মসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। পূর্ব নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারবে নিজেদের কালচারকে টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে। নিজের কালচারকে টিকিয়ে রাখতে হলে নিজেদের মাঝে আত্মসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে, ঠিক যেভাবে ওরিয়েন্টালিজমের মাধ্যমে পশ্চিমারা নিজেদের আত্মসচেতনতা গড়ে তুলেছে।
হাসান হানাফি পশ্চিমের সঙ্গে ইসলামী বিশ্বের সাক্ষাৎ ও বোঝাপড়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এই পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে পাঁচটি প্রধান উপাদান চিহ্নিত করেছেন, যেগুলিকে আবার দুইটি দিক বা উৎসে ভাগ করা যায়—
- দুইটি ইসলামি উৎসভিত্তিক
- তিনটি পশ্চিমা উৎসভিত্তিক।
ইসলামিক উৎসভিত্তিক
- যখন পশ্চিমের মধ্যযুগ চলছিল, তখন আব্বাসি খেলাফতের অধীনে গ্রিক দর্শনশাস্ত্র আরবি ও সিরিয়াক ভাষায় অনুবাদ হচ্ছিল। আর এই পারস্পরিক সম্পর্ক কোনো সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে আসেনি, জ্ঞানচর্চার ভিতর দিয়ে এসেছে। ইসলামি পণ্ডিতরা জ্ঞানগুলো চর্চা করে পশ্চিমের সাথে বোঝাপড়া করেছেন। এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় দেখা যায় যে, ইসলাম বা মুসলিমরা পশ্চিমকে পশ্চিমের আদলে বোঝার চেষ্টা করেছেন। আর এজন্য তারা পশ্চিমে গিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন গ্রিকরা নিজেদের সম্পর্কে কোন জ্ঞান গড়ে তুলেছে, সেই জ্ঞানটিকে তারা আত্মস্থ করেছে।
কিন্তু ওরিয়েন্টালিজমে হুবহু এর বিপরীত হয়েছে। এখানে পূর্ব সম্পর্কে তাদের যে ধারণা ছিল সেটিকেই তারা গড়ে তুলেছে এবং এর আলোকে সবকিছু বিকৃত করার চেষ্টা করেছে।
- পশ্চিমের সাথে বোঝাপড়ার দ্বিতীয় মাধ্যম হয়েছিল আন্দালুস। প্রথম ধাপে বোঝাপড়াটি হয়েছিল একদম খেলাফতের কেন্দ্র বাগদাদ থেকে। দ্বিতীয় ধাপে তখন বোঝাপড়া হয়েছে, মুসলিমরা যখন আন্দলুসে গিয়েছে এবং সেখানে ব্যাপকভাবে সভ্যতা গড়ে তুলেছে। আন্দালুস যেহেতু ইউরোপের ভিতরেই আর একদম অক্সিডেন্টের কাছাকাছি ছিল, তাই এই বোঝাপড়া সম্ভব হয়েছিল। এই যুগটিকে হাসান হানাফি বলেছেন স্কলাস্টিক যুগ। আর এর সময়টি হচ্ছে ১৩ শতক। এগারো বা বারো শতকে ক্রসেড সংঘটিত হয়েছে। ক্রুসেডাররা যখন মিশর, ফিলিস্তিন বা সিরিয়াতে এসেছে, এখানে গ্রিক জ্ঞান বা দর্শনগুলো সহজলভ্য ছিল। গ্রিক জ্ঞানগুলো যা আরবিতে অনুদিত, যা ক্রুসেডারদের কাছে ছিল না, তা তারা সাথে করে নিয়ে গিয়েছে। এর মাধ্যমে পশ্চিম বুঝতে পেরেছে যে, এই অঞ্চলে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্য আছে।
এর মাধ্যমে পশ্চিমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার জন্ম হয়, কারণতারা যে গ্রিক জ্ঞান অর্জন করছে, তার মূল মাধ্যম হচ্ছে আরবি অনুবাদ। এই উপলব্ধি থেকে পশ্চিমা চিন্তাবিদদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয় যে, গ্রিক জ্ঞানকে সরাসরি বোঝার জন্য আরবি ভাষার উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে এবং মূল গ্রিক উৎস থেকেই তা আত্মস্থ করতে হবে।
১৩শতকের দিকে এই বোধের বিকাশ ঘটে, যা এক নতুন জ্ঞান-আন্দোলনের সূচনা করে। গ্রিক জ্ঞানকে সরাসরি আত্মস্থ করার এই যুগটিকে ‘স্কলাস্টিক যুগ’ (Scholastic Era) বলা হয়।
এই সময়েই ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমের আরেকটি অর্থবহ বোঝাপড়ার সূত্রপাত ঘটে। মুসলিমদের অনুবাদকৃত দর্শন, চিকিৎসা, গাণিতিক ও বিজ্ঞানচর্চার নানা রচনাগুলো পশ্চিমা চিন্তাবিদরা পাঠ করে এবং সেগুলোর মধ্য দিয়ে তারা গ্রিক দর্শনের গভীরে প্রবেশ করে।
পশ্চিমের সাথে ইসলানের এই সম্পৃক্ততা ছিল মূলত একাডেমিক ও জ্ঞানভিত্তিক। ইসলাম-পশ্চিম সম্পর্কের এই পর্যায়টিকে তাই দ্বিমুখী এক বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিময় হিসেবেই দেখা যায়।
পশ্চিম ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার যে তিনটি মাধ্যম ছিল, তা হলো-
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ এবং পরবর্তী সময় ছিল মুসলিমদের জন্য একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অধ্যায়। এই সময়ে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের (Byzantine ও Sassanid) সঙ্গে মুসলিমদের সংঘাত সংঘটিত হয়, যা কেবল সামরিক দ্বন্দ্ব ছিল না, বরং ছিল বহুমাত্রিক রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতিফলন।
এই সংঘাতের মাধ্যমে পশ্চিম প্রথমবারের মতো মুসলিমদের অস্তিত্ব ও শক্তিকে চিনতে শুরু করে। হাসান হানাফি এই সময়কে ‘Greek এবং Roman Empires’-এর প্রেক্ষাপটে মুসলিম-পশ্চিম মুখোমুখি অবস্থানের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
- দ্বিতীয় মাধ্যমটি ছিল ক্রুসেডের যুগ। এই সময় পশ্চিমা খ্রিস্টান সাম্রাজ্য মুসলিম ভূখণ্ডে সরাসরি প্রবেশ করে এবং দীর্ঘদিন ধরে সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এই সংঘর্ষমূলক যোগাযোগের মাধ্যমেই পশ্চিমের মধ্যে মুসলিম সমাজ, সংস্কৃতি এবং ধর্ম সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে।
- তৃতীয় মাধ্যমটি হলো আধুনিক বা সমকালীন যুগ, যাকে হাসান হানাফি ‘Pax Americana’ এবং ‘Pax Europaea’ নামে চিহ্নিত করেছেন। এই পর্বে ইউরোপ ও আমেরিকা যৌথভাবে বিশ্ব রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছে। এই সময়টিকে তিনি পশ্চিমের পক্ষ থেকে মুসলিম বিশ্বকে বোঝার তৃতীয় প্রধান মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই যুগটিতে মূলত ঔপনিবেশিক পর্ব (Colonial Era) থেকে শুরু হয়েছে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো মুসলিম ভূখণ্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘ সময় ধরে দখল, শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ চালিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের ঔপনিবেশিক আধিপত্য ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং তার শূন্যস্থান পূরণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ফলে গত দুই শতাব্দী ধরে ইউরোপ ও আমেরিকা সম্মিলিতভাবে বিশ্বব্যবস্থাকে, বিশেষত মুসলিম বিশ্বকে, অস্ত্র, দখল এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে শাসন করে আসছে। এটি পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে মুসলিমদের অবস্থান নির্ধারণের তৃতীয় ধাপ।
হাসান হানাফির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, পশ্চিমের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের সংঘাতপূর্ণ তৃতীয় পর্বের প্রতিক্রিয়াতেই ‘অক্সিডেন্টালিজম’ ধারণার জন্ম হয়। এই পর্বে পশ্চিমের উপনিবেশবাদী দখল, সাংস্কৃতিক আধিপত্য ও সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্বে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ও আত্মপরিচয়ের চেতনা গড়ে ওঠে।
পূর্বের জনগোষ্ঠী, যারা দীর্ঘদিন ধরে অধিকারহীন ও দমিত অবস্থায় ছিল, তারা ধীরে ধীরে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে এবং প্রশ্ন করতে শুরু করে যে,পশ্চিমের জ্ঞান, সংস্কৃতি ও ক্ষমতা-কাঠামোর প্রকৃতি কী?
এই আত্মসচেতনতাই গড়ে তোলে ডি-কলোনাইজেশন প্রক্রিয়ার ভিত্তি, যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অক্সিডেন্টালিজম। এটি শুধু একটি তাত্ত্বিক ধারণা নয়; বরং একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রকল্প, যার মাধ্যমে পূর্ব নিজস্ব চেতনা, ঐতিহ্য ও ইতিহাস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে।


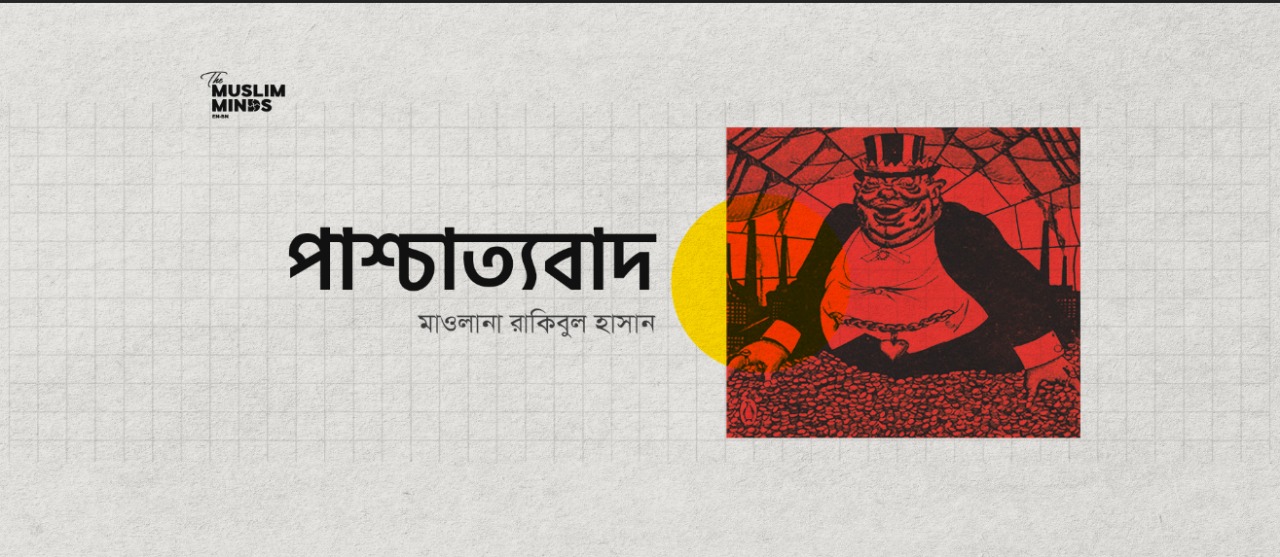


Leave a comment